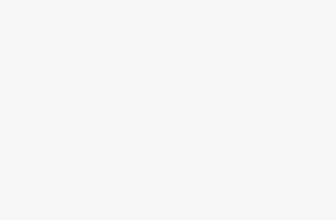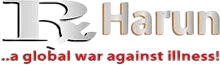মতিউর রহমান রেন্টু একটা বই লিখেছিলেন
আমার ফাঁসি চাই এই নামে এই নামটা উনি
দিছিলেন এইজন্যই যে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা
আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হাসিনার
একজন গুণমুগ্ধ ছিলেন সেই রেন্টু ভাই যখন
হাসিনার ঘনিষ্ঠ হইয়া তার পৈশাচিক রূপ
দেখলেন তিনি তার পুরা পলিটিক্যাল জার্নির
জন্য নিজেরই দায়ী করলেন তিনি ভাবলেন আমি
কেন এই ভুল করলাম এই দায় আমার তাই আমি
আমারই ধ্বংস চাই আমারই ফাঁসি চাই আমি ঠিক
এইভাবেই আমি নিজে চিকিৎসক ডাক্তার
ভালোবেসেই চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ছি আর এই
চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে অন্ধকার দিক দেখছি
যার মধ্যে কাজ করছি তার ফলে আমার নিজের
ফাঁসি নিজে চাওয়া ছাড়া মনে হয় মুক্তি
নাই তবে আমি এটাও মনে করি যেকোনো দেশের
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে ওই দেশে
পরিবর্তনের চাবিকাঠি লুকায় আছে আমি
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকট নিয়ে কথা
বলতেছি এই সংকট কাটানোর জন্য এক বিপুল কাজ
আমাদের করতে হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য
ব্যবস্থার সংকট এবং সেটা থেকে উত্তরণের পথ
নিয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে একটা কমিটি হইছে
তারা কাজ করতেছেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব
আছেন আমার বন্ধু এবং গুরুজনেরা তাই এটা
আমার দায়িত্ব আমি ব্যবস্থার সংস্কার
নিয়ে আমি এই মন্ত্রণালয়কে এই সংস্কার
কমিটিকে আমি সাহায্য করব দুইটা এপিসোড
করছি আরো করব আমি খুবই অবাক হয়েছি অসংখ্য
মানুষ সে এপিসোড গুলো দেখছে তার মানে
স্বাস্থ্যের মত বিষয় মানুষের বিশেষ
আগ্রহের জায়গা বাংলাদেশের পুলিশ আর
ডাক্তারেরা কিছু মনে করবেন না বাংলাদেশে
এমন কোন পরিবার নাই যারা স্বাস্থ্য
ব্যবস্থা বা পুলিশ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নাই তার মানে এই দুই জায়গায় কি বিপুল আর
ব্যাপক মনুমেন্টাল টাস্ক আছে সংস্কারের
সেটা সংশ্লিষ্টরা বুঝতে পারতেছেন কিনা
জানিনা কিন্তু আমার মনে হইলো যে আমি যেই
পাটাতনে দাঁড়ায় সলিউশন গুলো দিয়ে
বলতেছি আগের দুই এপিসোডে সেই পাটাতনে না
দাঁড়াইলে আমার সলিউশনটা আমি কেন দিছিলাম
সেটা বোঝা যাবে না আমার সলিউশন কোন সেন্স
মেক করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না যে
ইতিহাসবোধের উপরে দাঁড়ায় আমি সলিউশন
গুলোর কথা বলতেছি সেই একই ইতিহাসবোধের
উপরে আপনারাও দাঁড়ান ডাক্তাররাও দাঁড়ায়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাঁড়ায় সংস্কার
কমিটি দাঁড়ায় আসেন আমরা আদি ইতিহাস থেকে
শুরু করি চিকিৎসা ব্যবস্থা আর তার
বিবর্তনের ইতিহাস দেখি কোন ভাঙ্গা গড়ার
মধ্যে দিয়ে গেছে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ
আমরা যার উত্তরাধিকার এই চিকিৎসা
ব্যবস্থার ফিলোসফিক্যাল জার্নিটা কি আসেন
সেইটা আমরা বুঝে
দেখি সারা দুনিয়াতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার
মেরুদণ্ড চিকিৎসক অথচ এই চিকিৎসকদের
বিরুদ্ধে মানুষের পর্বত প্রমাণ অভিযোগ যে
সুস্থ হয়ে বাড়ি যায় সে অভিযোগ করে যে
যায় না সে তো করবেই তবে এই যে অভিযোগ
গুলা এটা যে শুধু বাংলাদেশে তা না এটা
সারা দুনিয়ার চিত্র কারণটা কি কারণটা
হইছে যে চিকিৎসা শুধু বিজ্ঞান না এটা একটা
আর্ট সেবাগ্রহীতা হিসেবে থাকে একজন রক্ত
মানুষের জীবন্ত মানুষ সে মানুষটা বাকি সব
মানুষের চাইতে আলাদা তার আলাদা জীবন আছে
সম্পর্ক আছে স্মৃতি আছে শিক্ষা আছে এই
বিপুল বৈচিত্রকে মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে
দক্ষতা দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে ম্যানেজ করাটা
খুবই জটিল একটা একটা কাজ এই জটিল কাজটাই
করেন ডাক্তার 2008 সালে হলিউডে একটা
সিনেমা হইছিল নাম নাইট সিন রোদান্ত সেই
সিনেমার নায়ক রিচার্ড টেফানি গ্যাংর
অভিনয় করছেন একজন ডাক্তারের ভূমিকায়
সিনেমায় ওই ডাক্তারের নাম হচ্ছে ডাক্তার
ফ্লেনার ডাক্তার ফ্লেনারের হাতে সার্জারির
সময় তার এক বৃদ্ধা রোগী সার্জারির বেডেই
মারা যায় ডাক্তার ফ্লেনার আসছেন সমুদ্রের
ধারে একটা শহর রোদান্ততে বৃদ্ধার স্বামীকে
কৈফিয়ত দিতে ফ্লেনার বলতেছে যে
জটিলতায় 50000 জনের মধ্যে একজনের এরকম
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যেই দুর্ঘটনাটা তোমার
স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটছে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ
করে শুইনা বললেন যে 50000 একজন একটা
সংখ্যা আমাদের 43 বছরের দাম্পত্য জীবন
আচ্ছা ডাক্তার তুমি কি আমার স্ত্রীর চোখের
তারার রংটা দেখছিলা এই যে আবেগের তীব্রতা
সেটা ডাক্তার ফ্লেনার সামাল দেবে কিভাবে
যদি না দুই পক্ষের বিশ্বাস আর এমপ্যাথির
একটা সম্পর্ক তৈরি না হয় পৃথিবীর কোন
পেশাকেই তো এমন তীব্র মানবিক আবেগ
মোকাবেলা করতে হয় না আমার ডাক্তার হওয়ার
মোটিভেশন বগুড়ার তারা ডাক্তার বাবারা
বন্ধু ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন
অসম্ভব রূপবান এক মানুষ ছিলেন এমন মমতায়
উনি রোগী দেখতেন এমন অপূর্ব ছিল উনার হাসি
উনার উপস্থিতি রোগ অর্ধেক ভালো করে দিত
উনি যখন বগুড়া আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠের
পাশের রাস্তা দিয়ে স্টেথো গলায় ঝুলায়
যাইতেন হাঁটতেন তখন মনে হইতো দুনিয়ার
সমস্ত সৌন্দর্য উনার উপরে ভর করছে আমারও
ছোটবেলায় মনে হইতো ঠিক এইভাবে স্টেথো
গলায় আমাকে মাঠের পাশ দিয়ে হাইটে যেতে
হবে ডাক্তারি পেশা এতটাই সেলিব্রেটেড ছিল
কান খেতে ছিল আমি ডাক্তার হইতে হইতে সেই
দিনগুলো কোথায় যেন হারায় গেল আমরা মনে
করি যে ডাক্তারেরা সব দেশে সব যুগে সব
সমাজে সমাদৃত ছিল কথাটা ঠিক না পৃথিবীর সব
দেশেই সমাজপতিরা চিকিৎসকদের প্রতি ছিলেন
নির্দয় এই ভারতবর্ষে চিকিৎসকরা রোগীর
বাসার সামনে দরজা দিয়ে ঢুকতে পারতেন না
তাদের ঢুকতে হইতো যেই পথে যেই পথে মেথরেরা
বাসার বর্জন নিয়ে যাইত গ্রিসের চিকিৎসককে
মনে করা হতো নিচু জাতের কারিগর রোমান
সাম্রাজ্যের চিকিৎসকদের কাজ দেওয়া হতো
দাসদের শেক্সপিয়ার চিকিৎসকদের চিটারস
মাউন্টেব্যাক্স বলছেন মাউন্টেবক্স মানে
প্রতারক আর কি ভলতিয়ার বলছিলেন চিকিৎসক
তারাই যাদের ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞান সামান্য
রোগ সম্পর্কে আরো কম আর রোগী সম্পর্কে
কিছুই জানে না সেই ভলতেয়ার যিনি এক
বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের জমিন তৈরি করবেন
আধুনিক দুনিয়ায় সেই ভলতে আর ডাক্তারদের
কি ভাবতেন দেখেন 1301 সালে বাংলা
সাহিত্যপত্র চিকিৎসা সম্পর্কে লিখতেছে এখন
দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন লোক জমিদারী
সেরেস্তায় কার্য করিতেন অথবা পন্ডিতি
করিয়া আসিতেছেন মধ্যে খেয়াল হইলো
নিদানশাস্ত্র পরি তিনি নিদান শাস্ত্র
কিছুদিন পড়িয়া বিশেষ একটি উপযুক্ত
সাইনবোর্ড লিখিয়া একজন সুচিকিৎসক হইয়া
পড়িলেন ব্যাবিলনের শাসক হাম্বুরাবি একটা
অদ্ভুত আইন করছিল সার্জারিতে ভুল হইলে
ডাক্তারের হাত কেটে নেওয়া হবে মধ্যযুগে
পশ্চিমা সাহিত্য বাঁচাল ভার অর্থলোভী
অপদার্থ চিকিৎসকদের নিয়ে কৌতুকের
ছড়াছড়ি কোকাচ্চিওর ডেকামের বা চসারের
ক্যান্টামেরি টেলস এইগুলোতে ডাক্তার একটা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চতুর্দশ
শতাব্দীর কবি পেত্রাক পোপ ষষ্ঠ
ক্লিমেন্টের অসুস্থতার কথা জাইনা উনাকে
দেখতে গেছেন গিয়ে দেখেন যে পোপের বিছানার
পাশে ডাক্তার তিনি ফিরে গিয়ে পোপকে চিঠি
লিখলেন যে আপনার রোগসজ্জার পাশে ডাক্তারের
উপস্থিতি আমাকে সংকিত করেছে প্লিনির
সাবধান বাণী স্মরণ করুন ডাক্তাররা সারাতে
নয় মেরে ফেলতেই পটু ফরাসি নাট্যকার
মলিয়ের তার ব্যঙ্গ নাটকের মূল উপজীব্যই
ছিল ডাক্তারদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা
ইমাজিনের ইনভ্যালিড দ্যা ফ্লাইং ডক্টর
ডনজুয়ান ডক্টর কিউপিড ডক্টর ইনস্পাইট অফ
হিমসেলফ এই পাঁচটা নাটকে ডাক্তারদের পেশা
নিয়ে এত ব্যঙ্গ করা হয়েছে যে ডাক্তাররা
দেখলে লজ্জাই পাবেন জর্জ বার্নার শহর একটা
নাটক আছে ডক্টর দিলে মানা সেখানে বার্নার
শাহ ভূমিকা লিখছেন যে 100 টাকা পারিশ্রমিক
নাও বড় ডাক্তার কখনো 10 টাকা
পারিশ্রমিকের ডাক্তারের সাথে একমত হবেন না
কারণ সেক্ষেত্রে তার বাড়তি 90 টাকার
দাবিটা খেলেও হয়ে যায় নেপোলিয়ান
বলছিলেন যে মানুষ মারার অপরাধে পরলোকে
গিয়ে আমাদের মত সেনাপতিদের চাইতে ঢের
বেশি জবাবদিহি করতে হবে ডাক্তারদের টলসয়
ওয়ারান পিস লিখতেছেন ওখানে কৌতুক ভরে
খোঁচাদিয়া লিখতেছেন যদিও ডাক্তারেরা
চিকিৎসা করেছিল ওষুধ খাইয়েছিল রক্তমক্ষণ
করেছিল তবুও সে ভালো হয়ে উঠলো মানে তার
মারা যাওয়ারই কথা ছিল যেহেতু ডাক্তার
আসছে কিন্তু ইতিহাসে আরো আগে চিকিৎসকের
করার অদ্ভুত ক্ষমতাকে মানুষ কিন্তু বন্দনা
করছিল জনগণের রোগ থেকে আরো গোলাপের
আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হয়ে উঠছিল যে
চিকিৎসকের দেবতার আসনে বসানো শুরু করল
তারা
মিশনেটপ আইসিস
গ্রিসেক্লোপিয়াস ভারতে
ধন্যরী ধর্ম ইচ্ছা করতে শুরু করছিল
চিকিৎসকদের যীশু বলছিলেন যারা ঈশ্বরের
অবহেলা বা পাপ করবে তারা চিকিৎসকের হাতে
পাড়ার মত শাস্তি পাবে কিন্তু অলৌকিক
নিরাময়ের ক্ষমতা প্রদর্শন হয়ে উঠলো
মানুষের মন জয়ের অন্যতম উপায় যীশু নিজেই
রোগাক্রান্তকে নিরাময় করে তার ঐশ্বরিক
ক্ষমতা প্রমাণ দিছেন এমনকি গৌতম বুদ্ধ
এখনো ক্যাথলিক ফাদার হওয়ার শর্ত হচ্ছে
কমপক্ষে দুইটা অলৌকিক নিরাময়ের ক্ষমতা
দেখাইতে হবে চিকিৎসার সাথে অলৌকিকত্ব আর
চিকিৎসককে দেবত্ব আরোপ করার ফলে লাভ হইলো
না চিকিৎসকের বা চিকিৎসাবিদ্যার কারণ
চিকিৎসক তো দেবতা না তার মধ্যে কোন
ঐশ্বরিক ক্ষমতাও নাই চিকিৎসকের কাছে
মানুষের প্রত্যাশা এত উঁচুতে পৌঁছাইলো যে
সেদিন থেকে চিকিৎসকরা হেরে গেলেন সেই
খেলায় তারপরেই এইভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে
চিকিৎসকদের এই অবস্থা তবে এই অবস্থার আবার
পরিবর্তন হইলো অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ দিকে
তখন কলোনি মাস্টাররা যাচ্ছেন সারা
দুনিয়ায় নতুন নতুন যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই
আছে সেই প্রথম ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনীতে
নেওয়া হতে থাকলো তরুণ ডাক্তারদের ছড়ায়
ছিটায় থাকা ডাক্তাররা একটা সুসংগঠিত
বাহিনীর সদস্য হয়ে ছড়ায় পড়লো সারা
দুনিয়ায় মিশতে থাকলো সাধারণ মানুষের
সাথেও মানুষেরা দেখলো ক্ষমতাবান কিন্তু
মাটির কাছাকাছি মানুষ 19 শতকের মাঝামাঝি
সৎ আদর্শবাদী চিকিৎসকদের দেখতে শুরু করল
পৃথিবী সাহিত্য ছাপ পড়লো 1872 সালে
প্রকাশিত হলো জর্জ এলিয়েটের মিডল মার্চ
তার নায়ক এক অসাধারণ আদর্শবাদী চিকিৎসক
টারসিয়াস লিড গেট লেখা হলো মাদাম বেভারি
এনিমি অফ দা পিপল যা থেকে সত্যজিদ রায়
বানাইলেন গণসত্য সিনেমাটা ডক্টর প্যাস্কেল
অ্যারোস্মিথ সিটাল প্লেগ বাংলা সাহিত্য
লেখা হলো দত্তা পথের দাবি আরোগ্য নিকেতন
অগ্নি সিনেমায় উত্তম কুমারের সবচেয়ে
উজ্জ্বল চরিত্র অভিনয় ছিল ডাক্তারের
চরিত্র দেশপ্রেমিক আদর্শবাদী মহান পেশায়
প্রতি নির্লভ মহাপুরুষের প্রতিচ্ছবি সেই
সময়টাই ছিল চিকিৎসা পেশার স্বর্ণযুগ আর
আজকের বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার
সমস্যা আরো জটিল কারণ পুরা সিস্টেম ভয়াবহ
করাপশন ঢুকছে রোগী ধরা দালাল
ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কমিশন হাসপাতাল
গুলোর রোগী ধরা বাণিজ্য কিছু বড় বড়
ফার্মাসিউটি কোম্পানি একটা বড় অংশের
ডাক্তারদের সাথে মাসহার সম্পর্ক কিছু
ডাক্তারদের মারাত্মক পেশাগত অদক্ষতা
রোগীদের সাথে দুর্ব্যবহার আর এই
সিস্টেমটাকে টিকায় রাখার জন্য গড়ে ওঠা
কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী পরিস্থিতিকে
জটিল থেকে জটিলতর করে বলছে মানুষ বুঝতে
পারে যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ তাই সে
মাঝে মাঝে তার ক্ষোভ ঝাড়ে ফ্রন্ট লাইনে
থাকা ডাক্তারদের উপরে অভিযোগ ভুল চিকিৎসার
ডাক্তাররা কেন ভুল চিকিৎসা করে এর দায় কি
শুধু
ডাক্তারের whoও বলে যে পশ্চিমা স্বাস্থ্য
ব্যবস্থাতে 10% রোগী ভুল চিকিৎসার শিকার
হন চিকিৎসার ঝুঁকি থাকবেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ
এবং যত্নশীল চিকিৎসকেরও ভুল হইতে পারে
কারণ প্রত্যেকটা রোগাক্রান্ত শরীর আপন
বৈশিষ্ট্য অনন্য শরীর সবসময় বইয়ের
টেক্সট মাইনা চলে না এটাই বিজ্ঞান কিন্তু
এই যুক্তি মানুষ মানবে কেন যদি তা একটা
করাপ্ট সিস্টেমের মধ্যে থাকা একজন মানুষের
কাছে শোনে ডাক্তারদের সাথে আস্থার
বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করতে 2000 বছর
লাগছিল সভ্যতার এই ইতিহাস যদি ডাক্তাররা
জানতো তাহলে মাত্র 50 বছরের মধ্যে সেটাকে
ধুলিস্বাদ করে দিতে পারতো না সেই জন্যেই
স্বাস্থ্যের জন্য দরকার একটা ফাদার ফিগার
ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মত যে নিজে
ডাক্তার সমস্যাটা ভালো বুঝে আবার জনতার
সাথে সম্পর্কিত মানুষ তাকে বিশ্বাস করে
এমন ফিগার ছাড়া আপনি স্বাস্থ্যে কোন
সংস্কার করতে পারবেন না আমাদের দুর্ভাগ্য
যখন আমরা সংস্কার করতে যাচ্ছি তখন জাফর
ভাই আমাদের মাঝে নাই বিষয়টা আরো গভীরে
যাইয়া দেখি ডাক্তারদের তরফ থেকে তারা কোন
জটিল সমস্যার মধ্যে থেকে কাজটা করে সেটা
না জানলে শুধু দোষ দেয়া সমস্যার সমাধান
হবে
না প্রাচীনকালে চিকিৎসকরা রোগীর চিকিৎসা
করতে করতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন সেই
সঞ্চিত জ্ঞান তিনি পরের প্রজন্মকে দিয়ে
যাইতেন আর আজকে চিকিৎসক যখন রোগীকে
চিকিৎসা দেন রোগ নির্ণয় করেন সেই
চিকিৎসার পিছনে থাকে কোনো না কোনো গবেষণা
সেই গবেষণার উপরে ভর কইরা চিকিৎসক তার
সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু খুবই উদ্বেগের
ব্যাপার চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল
যেটা দাবি করা হয়েছিল অন্য গবেষকেরা সে
একই পরীক্ষা করে সেই ফল পাচ্ছেন না
বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করে বুঝি
বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা মূল বিষয় হলো
রিপ্রোডিউসেবিলিটি তার মানে যেকোনো
পরীক্ষা আবার করে দেখানো যেতে পারে বারবার
করলে একই ফল আসবে এখানেই বিজ্ঞানের সাথে
অন্য বিষয়ের তফাত সেই কারণেই যেখানে
এমনটা ঘটে না সেগুলোকে আমরা অবিজ্ঞানিক
বিষয় বলি আমি যদি দুই অনু হাইড্রোজেন আর
এক অনু অক্সিজেন কে মিশে তার ভিতর দিয়ে
বিদ্যুৎ চালনা করি তাহলে আমি পানি পাবো
এটাই আমার যদি গবেষণা হয় তাহলে আমার এই
পদ্ধতি ব্যবহার করে সবাই একইভাবে পানি
বানাইতে পারবে যতবার এটা করবে ততবারই একই
ফল আসবে এটাকে বলে রিপ্রোডিউসেবিলিটি আর
এটা যদি না ঘটে তাহলে বলতে হবে আমার
গবেষণাটা ভুল বা আমার পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক
একই পর্যবেক্ষণ অনেকবার করে দেখানোই হলো
বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান
সংক্রান্ত গবেষণায় ভয়ানক অবস্থা
প্রকাশিত গবেষণায় যা ফল পাওয়া যায় বলে
করা হচ্ছে তার বেশিরভাগই আবার নতুন করে
গবেষণা করলে আর পাওয়া যাচ্ছে না মানে
আগের গবেষণাটাই ছিল ভুয়া এটা সামান্য কথা
না কারণ এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে
চিকিৎসার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে সেই
চিকিৎসা লাখো লাখো লোককে দেওয়া হয়েছে এই
দায় কি তাহলে চিকিৎসকের 2011 সালে
আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাইকোলজিস্ট ব্রায়ন নোসেক তার সহকর্মীদের
নিয়ে সাইকোলজির প্রায় 100 টা গবেষণা
আবার করছিলেন এই কাজটা ইন্ডিভিজুয়ালি করা
হয় না কারণ বিজ্ঞানীদের যা দিয়ে উৎসাহ
দেওয়া হয় যেমন স্কলারশিপ পুরস্কার কমিটি
মেম্বারশিপ এগুলো পাইতে হলে চমৎকপ্রদ
গবেষণার ফলাফল দেখাইতে হয় তাই আগে হওয়া
গবেষণা নিয়ে কেউ আর কাজ করতে চায় না একই
কাজ আরেকবার করে দেখতে চায় না অবাক
ব্যাপারে 100 টা গবেষণার তিন ভাগের এক ভাগ
গবেষণার ফল ভুয়া মানে আগের ফলের সাথে
নতুন ফল মিলতেছে না 2015 সালে সাইন্স
জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই ফলাফল তিন
ভাগের এক ভাগ ভুয়া তাইলে এই গবেষণাগুলোর
উপর ভিত্তি করে যে চিকিৎসা তৈরি হয়েছিল
তার তিন ভাগের এক ভাগ ভুল হবেই যার দায়
চিকিৎসকের না অনেকে মনে করতে পারেন
সাইকোলজিতে মন নিয়ে কাইকারবা সে মন তো
আসলে অধরা ধরা যায় না তাই হয়তো এরকম
অবস্থা অন্যান্য শাখায় অবস্থা তো হয়তো
তেমন খারাপ না কিন্তু না 2011 সালে
বিখ্যাত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বায়ার
জানাইলো যে ক্যান্সার সংক্রান্ত অনেক
গবেষণা তাদের গবেষকরা আবার করে দেখছেন এবং
মাত্র চার ভাগের এক ভাগ গবেষণায় ফল
মেলাইতে পারছেন মানে 75 ভাগ ফল ভুয়া পরের
বছর আরেক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এমজেন
জানাইলো ক্যান্সার সংক্রান্ত বিখ্যাত 53
টা গবেষণার মধ্যে মাত্র ছয়টার ফল তারা
আবার মেলাইতে পারছে মানে শতকরা 89 ভাগ
গবেষণার ফল ভুয়া একজনের গবেষণার প্রাপ্ত
ফলের উপরে কাজ করে পরে কেউ একজন কাজ করে
এভাবে বিজ্ঞান আগায় চলে তাহলে জ্ঞান যা
গড়ে উঠছে তা কিসের উপরে গড়ে উঠছে ভুয়া
গবেষণা ব্রায়ন নসেক সেন্টার ফর ওপেন
সাইন্স বলে একটা প্রতিষ্ঠান করছেন তারা
ক্যান্সার সংক্রান্ত 50 টা নামকরা গবেষণা
প্রবন্ধের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখতে শুরু
করলেন 2012 সালে পাঁচটা পরীক্ষা তারা
করছিলেন প্রথমে তার মধ্যে মাত্র দুইটা
পরীক্ষার ফল মিলছে পুরা পরীক্ষা তাহলে এর
অর্থ কি এটা গবেষণা
ফাঁক ছিল যা আগেই ধরা পড়ার কথা ছিল অন্তত
প্রকাশিত হওয়ার আগেই তাহলে
চিকিৎসাবিজ্ঞান কার উপরে নির্ভর করবে এই
ভুল আর মিথ্যা গবেষণাকর্মের উপরে এগুলো
ছাপা হয়েছিল বিখ্যাত সব মেডিকেল জার্নালে
কিভাবে সেগুলো ছাপা হইলো এত রিভিউয়ার আছে
জার্নাল গুলোর তাদের কারো কাছে গবেষণায়
ফাঁক ধরা পড়লো না এই রিভিউ এর প্রসেসটা
বলি যারা এই বিষয়টা সম্পর্কে জানেন না
ধরা যাক আপনি একটা গবেষণার ফলাফল পাঠালেন
একটা জার্নালে ছাপানোর জন্য সেই লেখাটা
কয়েকজন সেই ফিল্ডের কয়েকজন প্রথিত
রিভিউয়ারের কাছে পাঠানো হবে রিভিউ করার
জন্য অনেকে পরীক্ষার খাতা দেখার মতো তারা
সেই গবেষণাটা পরীক্ষা করে দেখবেন গভীরভাবে
যে গবেষণাটা ঠিক আছে কিনা কিন্তু আসলেই কি
তারা খুঁটায় খুঁটায় দেখেন 1998 সালে
বিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ব্রিটিশ মেডিকেল
জার্নালের সম্পাদিকা ফিওনা গডলি একটা
দুষ্টামি করে পরীক্ষা করছিলেন তিনি একটা
মনগড়া প্রবন্ধ 200 জনকে পাঠাইছিলেন এবং
ইচ্ছা করেই আট ধরনের ভুল ঢুকায় দিছিলেন
কেউই আটটা ভুল ধরতে পারেনি 200 জনের কেউ
আটটা ভুল ধরতে পারেনি গড়ে সবাই দুইটা করে
ভুল ধরতে পারছিলেন ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস
এটা আগের যে উদাহরণ দিলাম সেখানেও দেখছেন
ওয়ান ফোর্থ গবেষণা আসলে ভালো তিন চতুর্থ
গবেষণা আসলে ভুয়া হারভার্ডের একজন
বিজ্ঞানী জন বোহান একটা ধুনফুন গবেষণা
পত্র পুরাটাই ভুয়া তিনি সেটা 304 টা
জার্নালে পাঠাইছিলেন সে বানায় বানায়
লেখা গবেষণায় লাইকেন জাতীয় একটা গুলমের
ক্যান্সার অধিক কার্যকারিতা নিয়ে তথাকথিত
গবেষণায় গাল গল্প করছিলেন আশ্চর্য কথা
কেউ এই গাল গল্প ধরতে পারেনি কেউ না
অর্ধেকের বেশি জানার লেখাটা উৎসাহ নিয়ে
ছাপতে চাইছিল কান্ড দেখেন এই যে ভুলগুলো
হচ্ছে তার যে ইচ্ছা করে করা হচ্ছে তা না
কেন এই ভুলগুলা হয় আমি সেই গভীর আলোচনায়
আর গেলাম না আপনাদের বিরক্তির উৎপাদন হবে
তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু
উদাহরণ দিয়ে বুঝার চেষ্টা দেওয়ার চেষ্টা
করি কিভাবে ভুলগুলা হয় যখন আমরা কোন
বিশেষ মতবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তখন
চারপাশের পৃথিবীর খবরাখবরের মধ্যে সেই
মতবাদের সমর্থন খুঁজি এটারে ইংরেজিতে বলে
কনফার্মেশন বায়াস যদি আমাদের সামনে রাখা
সেই তথ্যের মধ্যে আমরা মতবাদের সমর্থন
খুঁজে না পাই তখন খবরটাকে গাঁজাঘুরিয়া
বলে মনে করি বিজ্ঞানের জগতে এমনটা ঘটে
আমার
এর সাথে যদি তথ্য মিলে যায় সেটা ভুল
হইলেও আমরা অনেক সময় গ্রহণ করে ফেলি
ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল বলছে যে প্রকাশিত
গবেষণার মাত্র 5% পাতে দেওয়ার মতো গবেষণা
প্রত্যেক মিনিটে প্রায় দুইটা মেডিকেল
গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছে আর যারা প্রকাশ
করতেছে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার
কোম্পানি এলসাফায়ার পৃথিবীর সবচেয়ে নামি
মেডিকেল প্রকাশনা কোম্পানির বছরের সেলস
তিন বিলিয়ন পাউন্ড আর প্রফিট প্রায় এক
বিলিয়ন পাউন্ড এমনকি এরা ফার্মাসিউটি
কোম্পানি এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ট্রেস
ছাপায় আর 99% ডাক্তারেরা আসলে পড়ে না আর
বাকি 1% ডাক্তারেরা পড়তে পারে না
গবেষণাকর্ম তাই তাদের ইনফরমেশনের সোর্স
হয়ে ওঠে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আমার
কথা না গবেষণার কথা এই যে মেয়ে তাদের
গবেষণার ফাইন্ডিংস এভাবে লিখছেন যে
ক্লিনিশিয়ান রেয়ারলি
এক্সেসপ্রাইজ এন্ড ইউজড এক্সপ্লিসিট
এভিডেন্স ডাইরেক্টলি ফ্রম রিসার্চ অর আদার
ফরমাল সোর্সেস তার মানে হইতেছে চিকিৎসকেরা
গবেষণা বা ফরমাল সোর্স থেকে এভিডেন্স
কালেক্ট করে এর ফলে যারা মার্কেটিং আর
প্রমোশনে বিলিয়ন ডলার ডলার খরচ করে তাদের
প্রভাবে ডাক্তাররা এমন সব ওষুধ লেখে যা
ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত হয়েছে এর মধ্যে 1998
সালে আমেরিকার পাঁচটা ওষুধকে প্রত্যাহার
করা হয়েছিল যেগুলো রোগীর কোন উপকার তো
করেই না ক্ষতি করছিল তার মধ্যে ছিল
এলার্জির ওষুধ মেধ কমানোর ওষুধ কোন
প্রাণঘাতী রোগ চিকিৎসার ওষুধ কিন্তু না
কিন্তু এইটা যেই সময় বাজারে ছিল আমেরিকার
মানুষের 10% এই ওষুধগুলো কোনো না কোনো
সময় খাইছে এই ওষুধের এপ্রুভালের সময় যে
ডেটা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল ভুয়া এ
দায় তাহলে কার এমন মিথ্যা আর গাঁজাখরি
জিনিস গবেষণা বলে প্রকাশিত হয়েছিল নামকরা
জার্নালে 2001 সালে 40 টা গবেষণাকর্মকে
প্রত্যাহার করা হয়েছিল 10 বছর পরে এই
সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াইছিল 400 এর বেশি
অর্থাৎ মোট গবেষণার সংখ্যা বাড়ছিল মাত্র
দেড় গুণ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত উঁচু
মানের গবেষণার প্রায় 15%ই আদতে যাচ্ছে
টাইপের গবেষণা আমেরিকা সরকারের অফিস অফ
রিসার্চ ইন্টিগ্রিটি 2008 সালে ন্যাচার
পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা
2000 বিজ্ঞানীর গবেষণা তিন বছর ধরে নিবিড়
পর্যবেক্ষণ করে দেখে এর মধ্যে 200 টা
গবেষণায় জোচুরি আছে প্রিডেটরি জার্নাল
বলে মেডিকেল সাইন্সে এক ধরনের জোচুরি
জার্নাল হইছে যেখানে আপনি মোটামুটি যা
খুশি তাই ছাড়তে পারবেন শুধু কিছু নগদ
নারায়ণ ধরায় দিতে হবে আর কি সহকারী
অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক আবার সহযোগী
অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হওয়ার জন্য মানে
প্রমোশনের জন্য প্রকাশিত গবেষণা লাগে
বাংলাদেশে একসময় এক বিখ্যাত প্রফেসর
দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাস্থ্য
বিবেষক একটা নিবন্ধ জমা দিয়া অধ্যাপকের
পদ বাগায় নিছিলেন আমি হিসাব দিতে পারবো
না জার্নালে লেখা দিয়া কত অধ্যাপকের পথ
বাংলাদেশের ডাক্তাররা বাগায় নিছেন তবে
কেউ কেউ যে বাগাইছেন সে অনুমান অবশ্যই করা
যায় কারণ এই প্রিডিটরি জার্নালে আমার
বন্ধু দেশের ডাক্তারদের লেখাই 50% এর বেশি
ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি যদি চিকিৎসকের
ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টকে প্রতিস্থাপন করে
তাহলে রোগী কি চিকিৎসা পাবে গবেষণা নামে
ট্র্যাস যদি ভর্তে থাকে মাথায় কোনটা
গবেষণা আর কোনটা ট্র্যাস এটা বোঝার দক্ষতা
যদি না থাকে তাহলে রোগী চিকিৎসা পাবে রোগী
যে শুধু চিকিৎসা পায় না এটা সে তার কমন
সেন্স দিয়া বোঝে তাই তার ক্ষোভ মাঝে মাঝে
ছাইচাপা আগুনের মত উদগৃত হয় সে
স্বাস্থ্যকর্মীর উপরে ঝাঁপায় পড়ে
ডাক্তাররা সারা দুনিয়াতে কর্মক্ষেত্রে
হিংসার শিকার হন এ হিংসার বিস্তার এতই
বিশাল যে 2002 সালে whoও কে ওয়ার্ল্ড
রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এন্ড হেলথ প্রকাশ
করতে হয়েছিল whoওর মতে 38% চিকিৎসক এবং
স্বাস্থ্যকর্মী সারাজীবনে অন্তত একবার
ভায়োলেন্সের শিকার হন বিশাল ঘটনা
দুনিয়াতে কোন পেশার ক্ষেত্রে এটা ঘটে না
আমি আলোচনায় গভীরে যাওয়ার আগে আপনাদের
একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই খেয়াল
করলে দেখবেন ভায়োলেন্সের শিকার চিকিৎসক
এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সবগুলাই সরকারি বা
পাবলিক 2021 সালে বাংলাদেশের চিকিৎসক
নিগ্রহের যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা নিয়ে একটা
গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে
যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী কর্মক্ষেত্রে
ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে তার 91% সরকারি
ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী আউটডোর
সার্ভিসের 80 ভাগ আর ইনডোর সার্ভিসের 60
ভাগ দেয় প্রাইভেট সেক্টর অথচ কি অবাক
বিষয় পাবলিক সেক্টরের চিকিৎসক সংখ্যায়
কম সার্ভিস দেওয়াও বেশি পরিমাণে
ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে আমি যেদিনের
ভিডিও রেকর্ড করি সেদিনই চিকিৎসাবিজ্ঞানের
গবেষণা সংক্রান্ত ডেটাবেজ মেডলাইনে
ভায়োলেন্সের কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিলাম
দেখেন কি বিপুল পরিমাণে ভায়োলেন্স
সংক্রান্ত আলোচনা আর গবেষণা মেডিকেল মহরে
বাড়ছে এই গ্রাফে অবশ্য এটাও দেখতে পারবেন
যে চিকিৎসাবিজ্ঞান ভায়োলেন্স সংক্রান্ত
আলোচনা শুরুই হয়েছে 80 এর দশক থেকে এখন
প্রশ্ন হচ্ছে এই ভায়োলেন্স কিভাবে থামানো
যাবে তাহলে আমাদের দেখতে হবে ভায়োলেন্সের
উৎস কি বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাতে হেলথ
বাজেট 2012 সালের পর থেকে ক্রমাগত কমছে
এখন মোটামুটি জিডিপির 2% দক্ষিণ এশিয়া
এটা প্রায় 5% প্রাইভেট সেক্টরে চিকিৎসা
মেটাতে বছরে চার শতাংশ মানুষ দারিদ্র
নির্মাণ নিচে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে এক
বছরের দরিদ্র কমে এক থেকে 2% শুধু
চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে গিয়ে দারিদ্র
সীমার নিচে চলে যায় প্রত্যেক বছর 4%
মানুষ বাদরের তৈলাক্ত বাসবে ওঠার উপমার
সাথে এটার কিন্তু মিল আছে এর আবার গাল ভরা
একটা নাম আছে মেডিকেল পভার্টি ট্র্যাক বা
দারিদ্র ফাঁদ হারভার্ড মেডিকেল স্কুলের
সোশ্যাল মেডিসিনের শিক্ষক পল ফার্মার
এটাকে বলছেন স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এর
অর্থ হচ্ছে জাত ধর্ম লিঙ্গ বর্ণ বৈষম্য
রাজনৈতিক হিংসা যুদ্ধ সামাজিক অর্থনৈতিক
অসাম্য এসব কিছুই নির্ধারণ করে কে অসুস্থ
হয়ে পড়বে এবং মেডিকেল সার্ভিস নিতে
পারবে তার মানে আপনি একজন স্বাস্থ্যকর্মী
হইয়া এই বাজেটে কাজ কইরা নিজেই
স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্সের অংশ হচ্ছেন
রোগীরা স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্সের শিকার
হয় প্রথমে ডাক্তার না জেনে না বুঝে
স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্সের অংশ হয়ে যান
রোগীর সচরণেরা সেই স্ট্রাকচারাল
ভায়োলেন্সের ফিজিক্যাল এম্বডিমেন্ট হিসেবে
দেখে একজন ডাক্তারকে তাই পাল্টা আক্রমণের
লক্ষ্য আসে আপনি স্বাস্থ্যকে প্রায়োরিটি
না দিলে স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স কমবে না
আপনি দেখবেন এই জুলাই আগস্ট বিপ্লব
যোদ্ধাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলো
না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওই যে
প্রায়োরিটি মনেই করলো না যে কাজটা জরুরি
যে মন্ত্রণালয় 20 থেকে 25 হাজার আহত
ছাত্র জনতাকে সার্ভিস দিয়ে তৃপ্ত করতে
পারে না সে 18 কোটি জনতাকে কিভাবে তৃপ্ত
করবে এটাই তো ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের
জন্য অ্যাসিড টেস্ট স্বাস্থ্য যে জাতি
উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য
একটা পূর্ব শর্ত এটা না বুঝে আমাদের নীতি
নির্ধারকেরা না আমাদের হেলথের লিডাররা
বুঝাইতে পারে নীতি নির্ধারকদের এ বিষয়টা
বুঝে দেখি
2010 সালে একটা ইন্টারেস্টিং প্রবন্ধ
প্রকাশিত হয়েছিল নিউক্লিয়ার ওয়েপেনস
এন্ড নেগলেক্টেড ডিজিজেস দা 10 টু ওয়ান
গ্যাপ শিরোনামে এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে 11
টা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ 10 ট্রিলিয়ন
ডলারের বেশি ব্যয় করছে অস্ত্র তৈরি এবং
মেইনটেনেন্সে আর সারা পৃথিবীতে আসার 800
কোটি মানুষ কৃমিতে আক্রান্ত যে হয় তার
বেশিরভাগই নিম্ন বা মধ্যয়ের পারমাণবিক
শক্তিধর দেশ যেমন ইন্ডিয়াতে 14 কোটি চীনে
সাড়ে আট কোটি নেগলেক্টেড ডিজিজ
কন্ট্রোলের জন্য বরাদ্দ সারা দুনিয়ায় এক
বিলিয়ন ডলারের কম অর্থাৎ 10 ট্রিলিয়ন
ডলারের পারমাণবিক অস্ত্র সম্বারের 10000
ভাগের এক ভাগেরও কম 2010 সালে
ল্যান্ডসেটের দোসরা জানুয়ারি আরেকটা
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল নেগলেক্টেড
টপিক্যাল ডিজিজ বিয়ন্ড দা টিপিং পয়েন্ট
শিরোনামে ওখানে প্রবন্ধকার বলছে যে
ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের মাত্র 06
শতাংশ বরাদ্দ আছে নেগলেক্টেড টপিক্যাল
ডিজিজের জন্য মাইকেল মমার্ট এসব বিশ্লেষণ
করে বলছিলেন যে স্বাস্থ্য হইলো দীর্ঘ
সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি এবং ফলাফল এই
যে স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে
সাধারণ মানুষ যাদের এই ভায়োলেন্সে কোন
ভূমিকা নাই নাই কোন অবস্থিতিও নাই
বাংলাদেশের মানসিক চিকিৎসকরা সম্প্রতি
বলছেন যে বাংলাদেশের চারজনের মধ্যে একজন
মানসিক রোগে ভুগতেছেন প্রত্যেক বছর 10000
জন মানুষ আত্মহত্যা করতেছে এর কারণ হিসেবে
বেকারত্ব হতাশার কথা বলছেন ডাক্তাররা
সাহেবেরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন
তা হচ্ছে বিচারহীনতা তার মানে সাম্য এবং
ন্যায়বিচার শুধু রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের
জন্যই জরুরি না ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য
জরুরী ভায়োলেন্সের মেডিসিন নেসেসারি
পলিটিক্স অফ পাবলিক হেলথ প্রবন্ধে বলা
হয়েছে এই ভায়োলেন্সের ট্রিগারিং ফ্যাক্টর
গুলো সামাজিক এবং রাজনৈতিক ডাইমেনশন আছে
ভায়োলেন্সের প্রশ্নের সাথে জোড়ায় আছে
গ্লোবালাইজেশনের বিতর্ক আলমাতার প্রাইমারি
হেলথকেয়ারের ঐতিহাসিক ঘোষণায় স্বাস্থ্য
নিশ্চিত করার শর্ত হিসেবে শান্তি নিশ্চিত
করার কথা বলা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সংঘাত
বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল আর
নিরস্তীকরণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল
ডাক্তারের খুব একটা অন্তর্গত দার্শনিক
কন্ট্রাডিকশন আছে আপনি খেয়াল না রাখলেই
পা স্লিপ কাটবেন এটা যে শুধু ডাক্তারদের
বুঝলে হবে না এটা বুঝতে হবে সবাইকেই কত
ধরনের সূক্ষ সূক্ষ ফাঁদ আছে ট্র্যাপ আছে
পিছল জায়গা আছে যেটা আমাদের খুব গভীরভাবে
বোঝা দরকার তাছাড়া শুধু ডাক্তারদের দোষই
দেবেন কিন্তু ফল আসবে না সংস্কারের কথা
বলবেন সংস্কার হবে না কারণ মূল সমস্যার
গভীরে যেয়ে বুঝতে হবে কোথায় সমস্যা এই
যে মেডিসিন স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাবিদ্যা
এটার অন্তর্গত একটা হিংসার উপাদান আছে
একদিকে মেডিসিন আর্ট অফ হিলিং আরেকদিকে
রোগের হন্তারোগ দুই ক্ষেত্রেই মেডিসিনের
কেন্দ্রে আছে মানুষ মেডিসিনের ঐতিহাসিক
বিবর্তনের মাঝে অন্তর্গত যে দ্বন্দ্ব এবং
টানাপোরণ আছে এইটা নিয়ে দেরিদার একটা
লেখা আছে প্লেটোস ফার্মেসি নামে আগ্রহীরা
পড়ে দেখতে পারেন সেখানে তিনি বলছেন
ফার্মাকনিক এই শব্দটার অর্থ একদিকে বিষ
আরেকদিকে অমৃত বা নিরাময়কারী মেডিসিনও
তাই আবার দেখেন আমরা রোগকে দেখি বায়োলজির
দৃষ্টিতে কিন্তু রোগকে বায়োলজির দৃষ্টিতে
দেখার একটা বিপদ আছে যেমন হার্ট অ্যাটাক
হইলে হার্টে রক্ত চলাচলের কার্ডিয়াক
এনজাইমের মার্কার এগুলো দেখতে হয় না দেখে
উপায়ও নাই কিন্তু রোগী তো একটা
রোগাক্রান্ত দেহ না একজন জীবন্ত মানুষ
ডাক্তার তো একটা বায়োলজিক্যাল এন্টিটিকে
চিকিৎসা করতেছে না একটা বায়োসোশাল
এন্টিটিকে চিকিৎসা করে বায়োসোশাল থেকে
বায়োলজিকে যখন আলাদা করা হয় তখন হয়
এন্টিটির রিডাকশন এইভাবেই রিডাকশনেজম এর
উপরে দাঁড়ায় আছে আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা
তাই সোশ্যাল এন্টিটি যখন সামনে এসে
দাঁড়ায় তখন সেটাকে পৃথিবীর কোন দেশের
ডাক্তাররাই আর মোকাবেলা করতে পারে না আবার
আরেকদিকে দেখেন আমরা যখন অসুস্থ হয়ে
ডাক্তারের কাছে যাই বা হাসপাতালে যাই
সেখানে দেখা আমাদের ক্লিনিক্যাল হেলথ মানে
সেখানে ব্যক্তির শরীরটা দেখা হয় আবার
ধরেন এই কোভিড মহামারীর মহামারীর সময়
আমরা তখন পাবলিক হেলথের দৃষ্টিকোণ থেকে
দেখি যেখানে কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ সেই
সামাজিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ যা
পরিবেষ্টিত হয়ে মানুষ থাকে যদি দুই
ক্ষেত্রেই ডিসোশালাইজেশন সমান ভাবে
কার্যকর থাকে তাহলে দুই ক্ষেত্রেই যেটা
হয় সেটা হচ্ছে ডি হিউম্যান
এরিক ক্যাসেলের একটা বেশ পুরনো লেখা আছে
শিরোনাম হচ্ছে রিলিফ অফ সাফারিং সেখানে
তিনি বলছেন রোগাক্রান্ত হলে মানুষের
মানবসত্তার অনেক কিছুকে তছনচ করে দেয়
ব্যক্তির সমগ্রতাকে ভেঙে চড়ে সাফারিংস এর
জন্ম দেয় এই সাফারিংস এর বোঝার ক্ষমতা
আধুনিক মেডিসিনের নাই আমাদের টেক্সট বইকে
ঢেলে লিখতে হবে পুরা টেক্সট বই আর
শিক্ষাদানের পদ্ধতি না বদলাইলে
চিকিৎসাবিদ্যার রোগীকে বায়োসোশাল এন্টিটি
হিসেবে দেখতে পারবে না এইবার আসেন
হাসপাতাল
প্রসঙ্গে আমরা ডাক্তাররা সবাই হ্যারিসন
পড়ছি মেডিসিনের টেক্সট বই হিসেবে সেই খোদ
হ্যারিসনে হাসপাতাল সম্পর্কে বলা আছে
হাসপাতাল হচ্ছে একটা ইন্টিমিডিয়েটিং
এনভারনমেন্ট যেখানে রোগীর সেন্স অফ
রিয়ালিটিকে অল্টার কইরা দেয় এই সেন্স অফ
রিয়ালিটি হচ্ছে রোগীর ব্যক্তিময়তা মানুষ
হিসেবে তার এন্টিটি সেটা হারায় গেলে রোগী
তার নিজস্ব জগতকে হারায় ফেলে সে হয়ে
যায় একটা বেড বা কেবিন নাম্বার হাসপাতালে
এসে ব্যক্তিময়তা হারায় নৈব্য ব্যক্তিক
হয়ে যায় আমরা নিজেরা বলি না বেড নাম্বার
14 এর রোগী বেড কেবিন নাম্বার 1001 এর
রোগী বা অমুক প্রফেসরের রোগী বা
হাইপোথাইরয়েডের রোগীটা বা রোগীর সেই
হারায় ফেলা জগত এবং হাসপাতালের
নৈরব্যক্তিক কেস নাম্বার দিয়া সাজানো
জগতের দুর্বল লিংক হচ্ছে একজন ডাক্তার এবং
তার ব্যক্তিময়তা অথচ একজন ডাক্তার যখন
গড়ে উঠতে থাকে সে তার ব্যক্তিময়তা
হারায় ফেলতে থাকে তার জগত সম্পর্কে
রিয়ালিটি বদলাইতে থাকে বাইরন গুডের একটা
অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল স্টাডি আছে এই নিয়ে
শিরোনাম মেডিসিন রেশনালিটি এন্ড
এক্সপেরিয়েন্স অন এন্থ্রোপোলজিক্যাল
পারসপেক্টিভ এই বইয়ে তিনি দেখাইছেন যে
কিভাবে মেডিকেল স্কুলে শুধু নতুন শব্দই
শেখানো হয় না চিকিৎসা শিক্ষার্থীর এক
নতুন জগতকে নির্মাণ করা হয় একজন
শিক্ষার্থীর ভিজুয়াল মেটাফর বদলায় যায়
এনাটমির কাছে ত্বক যা অনুভূতির অঙ্গ তা
হয়ে ওঠে একটা শিক্ষার সামগ্রী যা
মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখার অবজেক্ট মধ্য
চিকিৎসাবিদ্যা চিকিৎসককে যে বিপুল জ্ঞান
সম্ভার দেয় তাতে রোগী নিজের দেহ এবং
অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা হীনমন্যতায় ভোগে
এটাকে দর্শনের ভাষায় বলা হয়
এপিস্টেমোলজিক্যাল হাইপোকন্ড্রিয়া এই
এপিস্টেমোলজিক্যাল হাইপোকন্ড্রিয়ার এক
ধরনের নমনীয় হিংসা এবং এই হিংসা ধারণ
করেন চিকিৎসক নিজেই আপনি খেয়াল করলে
দেখবেন কিছু ডাক্তার রোগীকে অবলীলায় বলে
আপনি বুঝবেন না আপনি কি ডাক্তার আমি নিজে
ডাক্তার হয়ে শুনি আপনি কি স্পেশালিস্ট
আমি যদি স্পেশালিস্ট হয়ে প্রশ্নটা করতাম
তখন কি বলতো আল্লাহই মালুম আর্থার
ক্লিনম্যানের একটা বই আছে বেশ পুরানো
কিন্তু প্রাসঙ্গিক বইটার নাম ইলনেস
ন্যারেটিভ তিনি বলছেন ডাক্তারদের সিলেবাসে
এই বিশ্বাস জন্মানো হয় যে ডাক্তারদের
জানা প্রয়োজন শুধু রোগের বায়োলজি রোগের
সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল কালচারাল
অ্যাসপেক্ট জানাটা জরুরি না ফলে একটা রোগ
যখন রোগীর জীবনে একাধিক অর্থ নিয়ে হাজির
হয় সেটাকে বায়োমেডিক্যাল মডেলের মধ্যে
ধরার চেষ্টা করা হয় তখন শুরু হয় প্রসেস
অফ ডিহিউম্যানাইজেশন অথচ আমরা যেদিকে
তাকাই না কেন চারিদিকে আছে মানুষ তার
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্তি অসাম্য নিয়ে
সে মানুষকে বাদ দিয়ে আমরা হামলায় পড়ি
তার রোগের উপরে রোগীর মধ্যে হাজির থাকা
বায়োসোশাল এন্টিটির বদলে রোগের উপরে
হামলায় পড়ার ঘটনা ঘটে মেডিকেল
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের নিপুন
পরিচালনায় কি এই মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল
কমপ্লেক্স 1980 সালের 23 অক্টোবর
নিউল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনের সম্পাদক
আর্ন রেনম্যান একটা সাড়া জাগানো প্রবন্ধ
লিখছিলেন দ্যা নিউ মেডিকেল
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স নামে তিনি
পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলছিলেন যে এই
মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আমাদের
ফিউচার মেডিকেল সিস্টেমের দখল নিয়ে নেবে
কিন্তু তারা আমাদের একচুয়াল হেলথ
প্রায়োরিটিকে গুরুত্ব দেবে না তাই কিন্তু
হইছে আজ প্রায় 11 ট্রিলিয়ন ডলারের
বাণিজ্য ক্ষমতা সম্পন্ন হেলথকেয়ার
ইন্ডাস্ট্রির প্রায়োরিটি কি এদের
প্রায়োরিটি টাকা চুল গাজানোর ওষুধ বা
পৌরুষ জাগ্রত করার ওষুধ টিবির ওষুধ আসেনি
আজ পর্যন্ত 50 বছর রিফার্ম পেজেসিন কিন্তু
টিবির ওষুধ হিসেবে আবিষ্কার হয়নি
লেপ্রোসির ওষুধ হিসেবে আবিষ্কার হয়েছিল
জানেন নিশ্চয়ই ফাইলিয়ার বা কৃমির ওষুধ
তৈরি হয় না আরেকটা জায়গায় যেখানে তারা
ওষুধ তৈরি করে সেটা হচ্ছে ক্যান্সারের
ওষুধ কারণ ক্যান্সার রোগীর পরিবার আর তার
স্বজনদের অসহায়ত্বকে ক্যাপিটালাইজ করে
সর্বোচ্চ মুনাফা তৈরির সুযোগ তৈরি করে
দেয় আর চিকিৎসা সেবায় যে মেটাফর ব্যবহার
করা হয় সেটাও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ডিএমএইজ
করে মেটাফর সবসময়
সামরিক কোভিড মরামারির সময় দেখছেন না
ডাক্তাররা বলতে কোভিড যোদ্ধা তাই 150 বছর
আগে যখন এন্টিবায়োটিক প্রথম একটা রূপ
আবিষ্কার হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল
ম্যাজিক বুলেট এমনকি হোমারের সময়
চিকিৎসায় সামরিক মেটাফর ব্যবহার করা
হয়েছে 1914 সালে ব্রিটিশ মেডিকেল
জার্নালে ক্যান্সারকে নৈরাজ্যবাদী এবং
ক্যান্সার কোষগুলোকে বলবিক কোষ বলা
হয়েছিল মানে টার্গেট মেটাফর গুলোকে
পলিটিক্যাল অপোনেন্টের নামে করা হইতেছে এই
যে যুদ্ধের মেটাফর ইউজ করলে রোগকে দেহ
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় ফলে রোগীর
সাফারিংস কোন বিবেচ্য বিষয় হয় না
বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে রোগীর দেহ থেকে
আলাদা রোগটা ফলে মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল
কমপ্লেক্সের যোদ্ধারা সকল যুদ্ধাস্ত নিয়ে
ঝাঁপায় পড়তে পারে 2016 সালে আমেরিকান
জার্নাল অফ বাইরে একটা পুরা সংখ্যা ছিল এই
মেডিসিনের যুদ্ধের মেটাফর ব্যবহার নিয়ে
সেই সমস্ত রোগেই যুদ্ধের মেটাফর ইউজ করা
হয় যেখানে মুনাফা গগনচুম্বি আপনি কখনো
দেখবেন না যে ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
বা কৃমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ডাক্তার সাহেবরাও
নিশ্চয়ই নিজেদেরকে ডায়রিয়া বা কৃমি
যোদ্ধা পরিচয় দেবেন না যদিও খুব আগ্রহ
নিয়ে নিজেদেরকে ক্যান্সার যোদ্ধা বলে
পরিচিত করতে চাইবেন মেডিসিনের এই গ্লোবাল
কালচারে ডাক্তারেরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে
বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং বাহক হয়ে যায়
হিংসার এক নতুন চেহারা আমাদের সামনে ভাইসা
ওঠে এমনকি দেহকে জাতি রাষ্ট্রের সাথেও
তুলনা করা হয়েছে রমেলি মার্টিনের একটা
ইমিউনোলজি বই আছে নাম
অফ ইমিউনোলজি বডি নেশন স্টেট যুদ্ধ যুদ্ধ
খেলা জমার জন্য উত্তম মেটাফরি বটে তাই না
ডাক্তারি পেশা তো কলঙ্ক কম কামায়নি
ইতিহাসে ডাক্তারেরা যারা জীবন নয় মৃত্যুর
দূত হিসেবে কাজ করছে এসব তো পৃথিবীর
মানুষের কালেক্টিভ মেমোরি থেকে হারায়
যায়নি নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে
ডাক্তারেরা কাজ করতো সেইসব ডাক্তারেরা
কিভাবে মৃত্যুর গবেষণা করতো সাবসিকুয়েন্ট
ট্রায়ালের 23 জন অভিযুক্ত মধ্যে 20 জনই
ছিল ডাক্তার ভাবা যায় নাজি হিসেবে বিচার
হচ্ছে 23 জনের মধ্যে 20 জন ডাক্তার
মৃত্যুদূষ সেই ডাক্তার জোসেফ মেগেলের কথা
আমরা জানি সে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে
পেট্রোল থেকে শুরু কইরা হেনো কেমিক্যাল
নাই যা বন্দীদের শরীরে পুশ না করতো
গবেষণার নামে এই বদমাইশ গ্রেপ্তারা
ব্রাজিলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে সেই
দিনগুলো কি শেষ হইছে না হয়নি তো 2004
সালে ল্যান্ডসেটে আবু গ্রাহিব কারাগারে
ডাক্তারদের সেই একই নাজি বদমাইশী নিয়ে
একটা আর্টিকেল ছাপা হইছে আবু গ্রাহিব ইটস
লিগেসি অফ মিলিটারি মেডিসিন নামে আরো
দুইটা আর্টিকেল আছে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল
অফ মেডিসিনে উইদাউট আর হোয়েন ডক্টরস গো টু
দুইটাই 2005 সালে প্রকাশিত আগ্রহীরা পড়তে
পারেন অনলাইনে আছে এই দুঃস্বপ্ন কি শেষ
হইছে না হয়নি এখন কি হারবার্ডে এখন
গবেষণা হচ্ছে কগনিটিভ নিউরোসাইন্সে কি
জন্য জানেন যারা আমেরিকান রাষ্ট্রের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে অর্থাৎ
হার্টকোট টেরোরিস্ট তারা দৈহিক আর মানসিক
অত্যাচারের ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে ভেঙ্গা
পড়তে পারে তার ব্রেইন ম্যাপিং করা
মস্তিষ্কের ফিজিওলজিতে কি কি
বায়োকেমিক্যাল পরিবর্তন ঘটে সেটা পরিমাপ
করা কি ভয়ানক অবস্থা আবার দেখেন দেহের
উপরে রাষ্ট্রের নিয়ত সবচেয়ে বড় বড় রূপ
হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার
সময় এমনকি এক্সিকিউশনের সময় ডাক্তার
যুক্ত হচ্ছে ইনজেকশন দিয়ে জলজ্যান্ত
মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে তাকে
ডাক্তার মারতেছে ডাক্তার হয়ে উঠতেছে
জল্লাদ কোন গ্লানি নাই একজন ডাক্তার তো এই
কাজ করতেই পারে না এটা মেডিকেল এথিক্সের
বাইরে সে ডাক্তার হিসেবে তার শপথ ভঙ্গ
করতেছে কারণ সে তো জীবন বাঁচায় সে জীবন
নেয় না 70 80 এর দশকে ডাক্তারেরা
বাংলাদেশেও বন্ধাত্মকরণ কর্মসূচি
বাস্তবায়ন করছে কেউ জিজ্ঞেস করে নাই এটা
ঠিক না কেউ বলে নাই কোন ডাক্তার বলে নাই
এটা এটা ঠিক না তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি
সক্ষম পুরুষ নারীকে বন্ধ করে দিছে
ডাক্তাররা নিজেরা নিজের হাতে জ্ঞানের কি
ধ্বংসাত্মক ব্যবহার চিকিৎসাবিদ্যার এই যে
অন্তর্গত কন্ট্রাডিকশন এটাই এই পেশার
মানবিক সম্ভাবনাকে স্ফুরিত হইতে দেয় নাই
অন্তর্গত গভীর হিংসার বোধ থেকে একজন মেগেল
তৈরি করে একজন জল্লাদ তৈরি করে হাজার
হাজার বন্দাকরণ কর্মী তৈরি করে যারা তাদের
পেশা নিয়ে গর্ব করে গবেষণার তথ্য লুকায়
রফেক কক্সে এর মত ওষুধ কোটি কোটি মানুষকে
খাওয়ায় দেয় বিনা গ্লানিতে খুব সহজেই
এরা বিগ কর্পোরেশনের অংশ হয়ে যায় তৈরি
হয় দানবীয় মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল
কমপ্লেক্স যার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা আর
মুনাফা আর মুনাফা এই হিংসাই হইতেছে সেই
বিপন্ন বিস্ময় অষ্টাদশ শতকের সার্জন এবং
অ্যানাটমিস্ট উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়
নেসেসারি ইন হিউম্যানিটি তিনি তার
ছাত্রদের বলতেন আর্ন এ নেসেসারি
ইনহিউম্যানিটি বাই ডিসেক্টিং দ্যাট ডেট
একটা বিখ্যাত বাংলা কবিতা আছে উইলিয়াম
হান্টারের মেটাফর্নিয়া মনে পড়তেছে কি
জীবনানন্দ দাসের কবিতা আরো এক বিপন্ন
বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা
করে আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত করে লাশ
কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই তাই লাশ কাটা
ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে এই
লাশ কাটা ঘর থেকেই শুরু হয় একজন
ডাক্তারের নেসেসারি ইনহিউম্যানিটি ওই
নেসেসারি ইনহিউম্যানিটি থেকে
চিকিৎসাবিদ্যা মুক্তি না পাইলে শতাব্দীর
পর শতাব্দী চেষ্টা করলেও পৃথিবীর কোন
দেশেই ডাক্তাররা কখনো মানুষের প্রিয়জন
হইতে পারবেন না হে স্বাস্থ্য
মন্ত্রণালয়ের নেতারা ডাক্তারি
অন্তর্গত দুর্বলতা ঐতিহাসিক স্খলন আর তার
সাথেই বিপুল মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল
কমপ্লেক্স এর সাথে লড়াই করতে
পারবেন আমি ভয় দেখাইতেছি না কাজটা কত
ব্যাপক আর বিপুল তা মনে করায় দিচ্ছি আর
কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পলিটিক্যালি
এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল তীক্ষ্ণ ভেদার
পপুলার লিডার পাইলে কাজটা সহজ হইতো এটা
ছাড়া যে পারবেন না তা না কিন্তু জানা
বোঝাটা খুব পরিষ্কার না হইলে আপনি কাজটা
এমনকি শুরু করতে পারবেন না বলবেন সংস্কার
হবে না সংস্কার